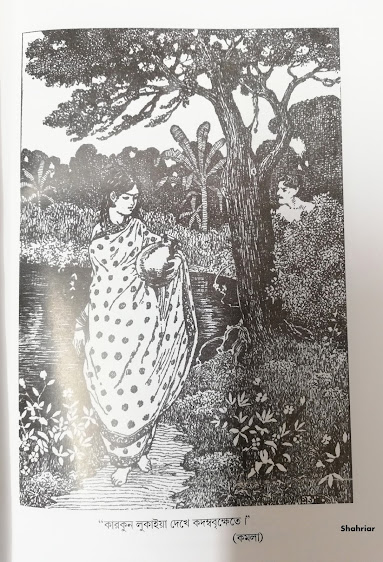ছবির ইতিহাস, ইতিহাসের ছবি (১৪ তম পর্ব)

|| মোহাম্মদ-ই-শিরান খিলজির সমাধি, মাহী সন্তোষ, নওগাঁ, বাংলাদেশ || ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ক্যাম্প বসল বরেন্দ্রভূমির আরেকটি হারিয়ে যাওয়া নগরী মাহী সন্তোষে। সেবারের দলে ছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কুমার শরৎকুমার রায়, অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, রমাপ্রসাদ চন্দ ও আরো কয়েকজন ইতিহাসপ্রেমী। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গাঁইতি ও কোদালের মাধ্যমে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হল বাংলার একটি গৌরবময় অধ্যায়। ইতিহাসের এ পাতাখানি সযত্নে লিখে রেখেছে পাল আমলের গৌরবময় সময় থেকে শুরু করে মুসলিম যুগের ইতিহাসের অনেক ঘটনাবলী। মাহী সন্তোষে সেবারের উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত হয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সব স্থাপনা ও অসংখ্য পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপনা হচ্ছে মোহাম্মদ-ই-শিরান খিলজির সমাধি। প্রাচীন কবরস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি একটি অতি প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের পাশে খুঁজে পায় একটি প্রাচীন জঙ্গলাকীর্ণ কবরস্থান, যেখানে অনেকগুলো কবরের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একটি কবর সবার নজর কাড়ে। ইতিহাসের নানা তথ্য-উপাত্ত মিলিয়ে এটিকে শিরান খিলজির সমাধি বলে চিহ...